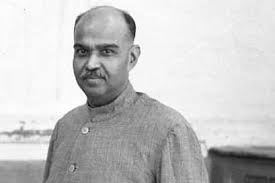নিউজ ডেস্ক: মুসলিম লিগের দ্বিজাতি তত্ত্ব মেনে ভারত ভাগ তখন অবশ্যম্ভাবী। নিজের অবস্থানে অনড় জিন্না। প্রধানমন্ত্রী হতে চান নেহরুও। তাদের জন্য কী দশা হতে পারতো বাংলার? কী হতো যদি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী না থাকতেন ? এর জন্য একটু পিছন ফিরে তাকাতে হবে। বুঝতে হবে, তিরিশ আর চল্লিশের দশক কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল বাংলার ইতিহাসে।
১৯৪০ এর দশক – ব্রিটিশ আর প্রকৃতির রোষে বাংলা
শ্যামাপ্রসাদ কীভাবে পশ্চিমবঙ্গের স্রষ্টা হলেন? তার জন্য আমাদের পিছিয়ে যেতে হবে স্বাধীনতার আগে। ১৯৪০ সাল। লাহোর অধিবেশনে মুসলিম লিগ পাশ করল দ্বিজাতি তত্ত্ব বিল। অর্থাৎ, মুসলিমদের জন্য দাবি করা হল আলাদা রাষ্ট্রের। শ্যামাপ্রসাদ তখন বঙ্গীয় হিন্দু মহাসভার সভাপতি। বাংলায় তখন মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক। তাঁর সঙ্গে জিন্নার মতবিরোধ তুঙ্গে উঠল। ফজলুল হকের সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করল মুসলিম লিগ। তখন ফজলুল হক মন্ত্রিসভাকে বাঁচাতে এগিয়ে এলেন শ্যামাপ্রসাদ। অবিভক্ত বাংলায় তখন জোর দেওয়া হল প্রজাদের মঙ্গলের ওপর। কিন্তু চক্রান্ত করতে শুরু করল ইংরেজ। এরমধ্যেই ১৯৪২ সালে শুরু হয়েছে ভারত ছাড়ো আন্দোলন। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে গর্জে উঠছে বাংলার বহু অঞ্চল। মেদিনীপুরে তৈরি হয়েছে সমান্তরাল জাতীয় সরকার। ব্রিটিশদের রোষ আছড়ে পড়ছে বাংলার ওপর। রোষ আছড়ে পড়ছে প্রকৃতিরও। ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত মেদিনীপুর সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চল। আছড়ে পড়ল মন্বন্তর। ত্রাণ কাজের অভাবে মন্ত্রিসভা থেকে ইস্তফা দিলেন শ্যামাপ্রসাদ। সুযোগ বুঝে ফজলুল হক সরকারকে বরখাস্ত করে খাজা নিজামুদ্দিনের নেতৃত্বে মুসলিম লিগকে ক্ষমতায় বসাল ব্রিটিশ।
দ্বিজাতি তত্ত্বের পাল্টা হিন্দু হোমল্যান্ড
এভাবেই বাংলায় কার্যত তখন মুসলিম রাজ। কয়েক বছরের মধ্যেই দেশভাগের দাবি প্রবল হচ্ছে। কালো হয়ে আসছে বাংলার আকাশ। কী হবে বাংলার? রাজনৈতিক ভাবে সওয়াল উঠছে, বাংলা চলে যাবে পাকিস্তানে। কেউ সওয়াল করছেন পৃথক বাংলা রাষ্ট্রের। সবমিলিয়ে অনিবার্য হয়ে উঠছে ভারত থেকে বাংলা ভাগের। এই পরিস্থিতিতেই এগিয়ে এলেন শ্যামাপ্রসাদ। ১৯৪৫ সালে লর্ড ওয়াভেল দেশ ভাগ নিয়ে রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেন। সেসময় তাঁর সঙ্গে আলোচনায় যোগ দেন মহাত্মা গান্ধী ও জিন্না। ১৯৪৬ সালে হিন্দু মহাসভার তরফে ব্রিটিশ মন্ত্রি মিশনের আলোচনায় যোগ দেন শ্যামাপ্রসাদ। তিনি দেশভাগের বিরোধিতা করেন। কিন্তু বুঝতে পারেন, আটকানো যাবে না ভারত ভাগ। তখন বাংলার হিন্দুরা যাতে ভারতে থাকতে পারে, সেই পথ খুঁজতে থাকেন তিনি। আওয়াজ তোলেন, যে যুক্তিতে দেশ ভাগ হয়েছে, সেই যুক্তিতেই প্রদেশ ভাগ করতে হবে। অর্থাৎ, হিন্দু প্রধান জেলাগুলিকে পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত করা চলবে না। এর জন্য গণ আন্দোলনও গড়ে তুললেন তিনি। বাংলা ভাগ নিয়ে ভোটাভুটিরও আয়োজন হল। ১৯৪৭ সালের ২০ জুন ভোটাভুটি হল অখন্ড বাংলা বিধানসভায়। সেখানে বাংলা ভাগের প্রস্তাব গৃহীত হল। তৈরি হল নতুন প্রদেশ পশ্চিমবঙ্গ। সেদিনের সেই ইতিহাসকেই গুরুত্ব দেয় বিজেপি। তাদের দাবি, আইনগত ভাবে ওই দিনই সৃষ্টি হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ। তাই পশ্চিমবঙ্গের জন্মদিন ২০ জুন। আর সেই অর্থেই, পশ্চিমবঙ্গের স্রষ্টা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।
১৯৩০ এর দশকে বাংলা…
গত শতাব্দীর ত্রিশের দশকের শুরু থেকে পঞ্চাশের দশকের প্রথম কয়েকটি বছরে— যুক্ত বঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দু’টি দশকে— শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক চরিত্র। ১৯৩২ সালের ব্রিটিশ সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইনের অঙ্গীভূত হল, বাংলার নির্বাচনে তার প্রয়োগ হতে চলল। বাংলার ৪৫ শতাংশ হিন্দুর জন্য (তফসিলি-সহ) বরাদ্দ হল ৩২ শতাংশ— ৮০টি মাত্র আসন, ২৫০ আসনের আইনসভায়। প্রতিবাদে সরব হল বাঙালি হিন্দু সমাজ। ১৯৩৬-এর ১৪ জুলাই টাউন হলে বিশাল সভায় সভাপতিত্ব করলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আহ্বায়কদের মধ্যে ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র রায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, সরলা দেবী, নীলরতন সরকার প্রমুখ। অসুস্থ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন, “বহুকাল পর আজ আমি রাজনৈতিক সভায় যোগদান করিলাম। প্রথমে এই সভায় যোগ দিতে আমি ইতস্ততঃ করিয়াছিলাম; কিন্তু স্বদেশের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া আমি আপনাদের আহ্বান উপেক্ষা করিতে পারিলাম না…।” ১৯৩৭-এর নির্বাচনে এই সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার আসন ভাগাভাগিতে এবং সর্বভারতীয় কংগ্রেসি নেতাদের অদূরদর্শী সিদ্ধান্তের ফলে বাংলায় শাসন ক্ষমতায় আসে মুসলিম লীগের সরকার। এখান থেকেই স্পষ্ট, বাংলায় হিন্দুদের কী হাল হতে চলেছে, তা নিয়ে আশঙ্কায় ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ।
কীভাবে রাজনীতিতে শ্যামাপ্রসাদ?
১৯৩৫-এর সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা অসুস্থ অরাজনৈতিক রবীন্দ্রনাথকে রাজনৈতিক সভায় উপস্থিত হতে যেমন বাধ্য করেছিল, তেমনই এর ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি বাধ্য করল বাংলার আর এক বিখ্যাত অরাজনৈতিক পরিবারের অরাজনৈতিক কৃতী ব্যক্তিকে ক্রমশ রাজনৈতিক মঞ্চে ভূমিকা পালনে। শ্যামাপ্রসাদ ১৯২৯-৩০’এ কংগ্রেস বা নির্দল প্রার্থী হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্র থেকে বঙ্গীয় আইনসভায় নির্বাচিত হন, কিন্তু তখনও রাজনৈতিক ভূমিকায় আসেননি। ১৯৩৪ থেকে ১৯৩৮— চার বছরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য থাকার সময়ই বুঝতে পারছিলেন, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ছায়া পড়ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গনেও। সুতরাং, তাঁকেও রাজনীতির মঞ্চে নামতে হল। ১৯৩৭ সালে আবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত নির্দল সদস্য হলেন বঙ্গীয় আইনসভায়। ওই বছরেই হিন্দু মহাসভায় যোগদান করেন তিনি। ১৯৩৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি-লিট উপাধি প্রদান করে। ১৯৩৯ সালে বিনায়ক দামোদর সাভারকারের সভাপতিত্বে কলকাতায় বসে হিন্দু মহাসভার অধিবেশন। সেখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ১৯৪০ সালে তিনি হিন্দু মহাসভার কার্যকরী সভাপতি নির্বাচিত হন। বছর কয়েকের মধ্যেই তিনি হন বাংলার অন্যতম প্রধান বাঙালি রাজনৈতিক নেতা।
দেশের প্রথম শিল্পমন্ত্রী শ্যামাপ্রসাদ
শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ১৯০১ সালের ৬ জুলাই তাঁর জন্ম। ১৯০১ থেকে ১৯৫৩ সাল। মাত্র ৫২ বছর বেঁচে ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। কিন্তু এই সময় জুড়েই তিনি গভীর দাগ কেটেছিলেন ভারতীয় সাহিত্য থেকে রাজনীতিতে। দেশের প্রথম শিল্পমন্ত্রী হিসেবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন শিল্প ক্ষেত্রেও। খড়গপুর আইআইটি থেকে কলকাতার প্রথম ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সোশাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট স্থাপনা তাঁরই মস্তিষ্ক প্রসূত। চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ স্থাপনের সিদ্ধান্তও তিনিই নিয়েছিলেন। ভিলাই ইস্পাত কেন্দ্র গড়ে ওঠার পেছনেও তাঁর পরিকল্পনা ছিল। দেশ স্বাধীনের পর হিন্দু মহাসভাকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাজে আত্মনিয়োগের পরামর্শ দেন শ্যামাপ্রসাদ। কিন্তু পরিস্থিতি বদলায় দ্রুত।
নেহরু মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ
১৯৫০ সালে পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার বেড়ে চলে। হত্যা, লুন্ঠন, নারীর সম্ভ্রমহানি নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৫০ সালের ১৪ এপ্রিল নেহরু মন্ত্রিসভার মন্ত্রী হয়েও এর প্রতিবাদে লোকসভায় গর্জে ওঠেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় । প্রধানমন্ত্রী নেহরুর সঙ্গে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলির চুক্তির বিরোধিতা করে পদত্যাগ করেন মন্ত্রিসভা থেকে। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর যুক্তি ছিল, মুসলিম তোষণ করতেই চুক্তি করেছিলেন নেহরু। যা বাঙালি হিন্দুদের আরও বিপদের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। যার ফলস্বরূপ, বাংলাদেশের হিন্দুদের ওপর নেমে এসেছিল অসহনীয় অত্যাচার।
প্রতিষ্ঠা করলেন জনসঙ্ঘ
১৯৫০ সালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে বেরিয়ে পরের বছরই তাই নতুন দল গঠন করেন শ্যামাপ্রসাদ। প্রতিষ্ঠা করেন জন সংঘের। বহু পথ পেরিয়ে ১৯৮০ সালে এই জনসংঘই ভারতীয় রাজনীতিতে আবির্ভূত হয় ভারতীয় জনতা পার্টি বা বিজেপি হিসেবে। কিন্তু জনসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস জানতে সমসাময়িক ভারতের ইতিহাস জানাটাও জরুরি। জানতে হবে, কেন প্রয়োজন হল কংগ্রেসের বিকল্প রাজনৈতিক দলের? ১৯৪৮ সালে গান্ধী হত্যার পরবর্তীকালে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘক নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ১৯৪৮ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি গ্রেফতার হন আরএসএস-এর সরসঙ্ঘচালক গুরুজি গোলওয়ালকর। দেশের রাজনীতির ক্ষেত্রে তখন কংগ্রেসের একচ্ছত্র আধিপত্য। কংগ্রেসের যে কোনও ভ্রান্ত নীতির বিরোধিতা করার জন্য সংসদের ভিতরে-বাইরে জাতীয়তাবাদী আওয়াজের প্রয়োজন হয়। দেশের আইনসভাগুলিতে কংগ্রেসের মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য হিন্দু জাতীয়তাবাদী ভাবধারা সম্পন্ন কোনও রাজনৈতিক দল ছিল না। এটা পরিষ্কার হয় যে শাসকের যে কোনও ভুল অথবা জাতীয়তাবাদ বিরোধী সিদ্ধান্তের মোকাবিলা শুধুমাত্র সামাজিক সংগঠনের পক্ষে সম্ভব নয়। এর পাশাপাশি সঙ্ঘকে নিষিদ্ধ করার পরে রাজনৈতিক দলের প্রয়োজনীয়তা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।
গোলওয়ালকর-শ্যামাপ্রসাদ বৈঠক
তৎকালীন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ভিতরেও রাজনৈতিক দল গঠনের কথা বলতে থাকেন অনেকেই। ১৯৪৯ সালেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ‘অর্গানাইজার’ পত্রিকার প্রধান সম্পাদক কেআর মালকানি, তাঁর নিজের লেখায় তুলে ধরেন রাজনৈতিক দল গঠন করা কেন প্রয়োজন। সঙ্ঘের তৎকালীন সরসঙ্ঘচালক গুরুজি গোলওয়ালকরকে তখন অনেকেই অনুরোধ করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘকে রাজনৈতিক দলে পরিবর্তিত করার জন্য। কিন্তু গুরুজি গোলওয়ালকর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সামাজিক কার্যপদ্ধতি বদল করতে চাননি। ১৯৪৮ সালের ২ নভেম্বর এক বিবৃতি দিয়ে সর সঙ্ঘচালক পরিষ্কার করে দেন যে আরএসএস-এর কোনও রাজনৈতিক লক্ষ্য নেই। এমন সময়েই গুরুজি গোলওয়ালকারের সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বৈঠক হয়, জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠার বিষয়ে। রাজনীতির ক্ষেত্রে গুরুজি কয়েকজন স্বয়ং সেবককে পাঠান। তাঁরা হলেন — দীনদয়াল উপাধ্যায়, অটল বিহারী বাজপেয়ী, লালকৃষ্ণ আদবানি, জগদীশ মাথুর, সুন্দরসিং ভাণ্ডারি প্রমুখ। শুরু হয় ভারতীয় জনতা পার্টির পূর্বতন ভারতীয় জনসঙ্ঘের যাত্রা। ১৯৫১ সালের ২১ অক্টোবর দিল্লির ‘রাঘোমাল আর্যকন্যা হাইস্কুলে’ প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতীয় জনসঙ্ঘ । প্রথম সভাপতি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।
জনসঙ্ঘের ইস্তাহারে দেশকে ভারতমাতা সম্বোধন
২১ অক্টোবর ১৯৫১ সালে পথ চলা শুরু হয় ভারতীয় জনসঙ্ঘের । প্রতিষ্ঠার দু’মাসের মধ্যেই পার্টিকে লড়তে হয় স্বাধীন ভারতের প্রথম লোকসভা নির্বাচন। প্রসঙ্গত, দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫১ সালের ডিসেম্বর মাসে। জনসঙ্ঘের নির্বাচনী ইস্তেহারে দেশকে ‘ভারত মাতা’ সম্বোধন করা হয় এবং ‘দেশের স্বার্থ সবার উর্ধ্বে একথা বলা হয়। ওই নির্বাচনী ইস্তেহারে আরও বলা হয়, দল ক্ষমতায় এলে গ্রামীণ অর্থনীতি মজবুত করা হবে, কৃষি ও শিল্পভিত্তিক অর্থনীতিতে জোর দেওয়া হবে। নির্বাচনী ইস্তেহারে ‘স্বদেশিয়ানা’র উল্লেখও করা হয়। দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে মোট আসন সংখ্যা ছিল ৪৮৯। এরমধ্যে ৯৩টি আসনে প্রতিদ্বন্দিতা করে ভারতীয় জনসঙ্ঘ ৩টি আসন পায়। এরমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ থেকেই এসেছিল ২টি আসন। দক্ষিণ কলকাতা থেকে জেতেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় , মেদিনীপুর থেকে দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। আর রাজস্থানের চিতোর থেকে জেতেন উমাশঙ্কর ত্রিবেদী।
নেতা শ্যামাপ্রসাদ
এভাবেই নিজে জিতে, দলকে নেতৃত্ব দিয়ে জনসঙ্ঘকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। কিন্তু কাশ্মীর সফরে গিয়ে আচমকাই মৃত্যু হয় তাঁর। এই মৃত্যুও রহস্যে মোড়া।
যদি ইতিহাস ঘুরে দাঁড়াত: নেহরুর ছায়া বনাম মুখার্জির সম্ভাবনা
১৯৪৭ সালের পর ভারত পেয়েছিল স্বাধীনতা, কিন্তু সেই স্বাধীনতা কোন পথে চলবে—তা নিয়ে শুরু হয়েছিল গভীর বিতর্ক। সেই বিতর্কের দুই মেরুতে ছিলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি।
নেহরু হয়ে উঠেছিলেন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী, আর মুখার্জি হয়ে উঠেছিলেন এক ‘বিকল্প ভারতের কণ্ঠস্বর’। আজ, এত দশক পর দাঁড়িয়ে, আমরা যদি ইতিহাসকে নতুন করে ভাবি—তাহলে একটিই প্রশ্ন সামনে আসে—
নেহরুর পথ না মুখার্জির পথ—কে দিতে পারতেন আরও ভারসাম্যপূর্ণ, আত্মবিশ্বাসী এক ভারত?
______
নেহরুর নীতিগত অবস্থানে প্রশ্ন
১. কাশ্মীর সিদ্ধান্ত: রাজনৈতিক না আবেগঘন?
নেহরুর সবচেয়ে বিতর্কিত সিদ্ধান্তগুলোর একটি ছিল কাশ্মীর নিয়ে তার নীতিনির্ধারণ। রাষ্ট্রীয় সংবিধানে ৩৭০ ধারা রেখে কাশ্মীরকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া, এবং কাশ্মীর ইস্যু আন্তর্জাতিক ফোরামে নিয়ে যাওয়া—আজও ভারতের জন্য একটা জ্বলন্ত সমস্যা।
২. চীন-নীতি ও ১৯৬২ সালের যুদ্ধ
নেহরুর “হিন্দি-চীনি ভাই ভাই” নীতির পরিণতি ছিল এক বিপর্যয়। ১৯৬২ সালে চীনের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য ভারত মোটেও প্রস্তুত ছিল না । চীন-নীতিতে অতিরিক্ত আস্থা এবং প্রতিরক্ষা খাতে অবহেলা ছিল এক ভয়ানক ভুল ছিল।
৩. সমাজতন্ত্রমুখী অর্থনীতি: অদৃশ্য হাতের অভাব
নেহরু বেছে নিয়েছিলেন রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত সমাজতান্ত্রিক মডেল—যেখানে প্রাইভেট সেক্টর প্রায় কোণঠাসা। তার ফলে ভারতের অর্থনৈতিক গতি শ্লথ হয়ে পড়ে। লাইসেন্স রাজ, আমলাতন্ত্র এবং দুর্নীতির বিস্তার ঘটায় এই মডেল।
৪. ধর্মনিরপেক্ষতার দ্বিচারিতা
নেহরু নীতিতে অনেকসময় সংখ্যাগুরু হিন্দু সমাজের উদ্বেগ উপেক্ষিত হয়েছিল। পাকিস্তান থেকে আগত হিন্দু উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনে নেহরু সরকার যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়নি—যেখানে মুখার্জি বারবার সরব হয়েছিলেন।
শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি: বিকল্প ভারতের এক বাস্তববাদী কণ্ঠ
ন্যাশনাল কনফারেন্স বা কংগ্রেসের বাইরে দাঁড়িয়েও শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি হয়ে উঠেছিলেন একটি শক্তিশালী দেশাত্মবোধী কণ্ঠস্বর। আজকের ভারতে তাঁর অনেক ভাবনা বাস্তবে পরিণত হয়েছে—যা তাঁর সময়েও প্রাসঙ্গিক ছিল।
১. ৩৭০ বিরোধিতা: “এক দেশ, এক বিধান”
শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী কাশ্মীরকে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে দেখতেন, এবং ৩৭০ ধারার বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, “এক দেশ—দুই বিধান, দুই প্রধান, দুই পতাকা—এ চলতে পারে না।পরবর্তীতে ২০১৯ সালে কেন্দ্রীয় সরকার ৩৭০ ধারা বিলোপ করে তাঁর বক্তব্যকেই বাস্তব রূপ দেয়।
২. উদ্বাস্তুদের হয়ে কথা বলা
পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত হিন্দু উদ্বাস্তুদের দুরবস্থার জন্য তিনি নেহরু-লিয়াকত চুক্তিকে দায়ী করেছিলেন। আজও পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরায় মুখার্জির উদ্বেগ বাস্তব বলে প্রমাণিত।
৩. কেন্দ্রীয় শক্তির সমর্থক
তিনি বিশ্বাস করতেন, একটি নবজাত রাষ্ট্রের পক্ষে শক্তিশালী কেন্দ্র দরকার। বর্তমান ভারতের কেন্দ্রীয় একীকরণ ও ‘cooperative federalism’-এর নীতিও অনেকটা এই দর্শনের সঙ্গে মেলে।
৪. ধর্মের রাজনীতি নয়, সংস্কৃতির আত্মপরিচয়
শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীকে অনেক সময় হিন্দু রাজনীতির প্রতীক হিসেবে দেখা হয়, কিন্তু তাঁর দর্শনের মূল কথা ছিল—সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়ের উপর রাষ্ট্র নির্মাণ। তিনি বিশ্বাস করতেন, ভারত তার সভ্যতা, ঐতিহ্য ও ইতিহাসকে অস্বীকার করে টিকে থাকতে পারবে না।
______
তাহলে প্রশ্ন—যদি মুখার্জির পথ বেছে নেওয়া হতো?
• ভারত আরও আগে ৩৭০ ধারা থেকে মুক্ত হতো
• ধর্মের ভিত্তিতে নয়, সংস্কৃতির ভিত্তিতে জাতীয় সংহতি গড়ে উঠত
• পাকিস্তান ও চীন নিয়ে বাস্তববাদী কূটনীতি থাকত
• অর্থনীতি হতে পারত আরও বেসরকারি উদ্দ্যোগমুখী
• ধর্মনিরপেক্ষতা থাকত, তবে ‘anti-majority’ চেহারা পেত না
এই সব যুক্তির প্রেক্ষিতেই মনে রাখতে হবে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীকে। তাঁর জীবনের কাহিনী শুধুমাত্র একজন রাজনীতিবিদের গল্প নয়। এটি এক “মানসিক রূপান্তরের ইতিহাস”, যা একটি জাতির ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে।